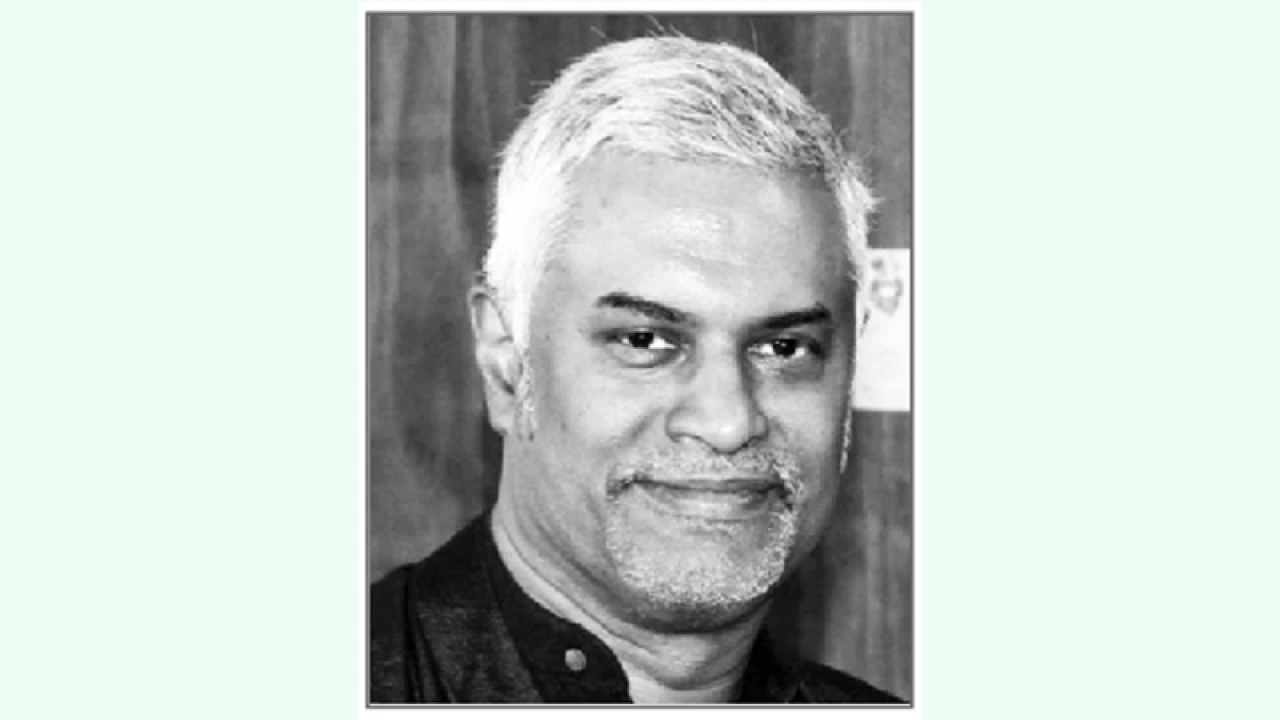ফিরে দেখা সিপাহি সংহতির পাঁচ দশক

জাতীয় সংহতি দিবসের এবার পঞ্চাশ বছর। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর দেশের ইতিহাসে এক দিকপরিবর্তনের দিন। এই দিনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে এক জটিল ও রক্তক্ষয়ী মুহূর্ত হিসেবে ফিরে আসে। ৭ নভেম্বর কেন্দ্রে ছিলেন কর্নেল আবু তাহের- এক এমন মানুষ, যার বুকে ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে জনমৈত্রীর এক হোসেন মিয়ার ‘ময়নার দ্বীপ’ গড়ার তীব্র আকাক্সক্ষা। কিন্তু হায়! তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি যে পথ বেছে নিলেন, তা ছিল যেন রঙিন চশমায় দেখা এক দুঃস্বপ্নের দৃশ্যপট। তাহেরের ভূমিকা ছিল এই মর্মান্তিক পরিণতির উচ্চাভিলাষী পথপ্রদর্শক হিসেবে।
তাহেরের সংগ্রাম ছিল বাস্তবতার জমিনে এক পরাবাস্তব বীজ বপন করার মতো। তিনি সামরিক শৃঙ্খলার বাইরে গিয়ে ইউরোপীয় সাম্যের এক অসম্ভব স্থাপত্য তৈরি করতে চাইলেন। তার হৃদয়ে ছিল মার্কসবাদী সাম্যের এক জ্বলন্ত আকাক্সক্ষা, যা ছিল যেন সালভাদর দালির ছবির নরম ঘড়ির মতো সময়কে নিজস্ব খেয়ালে বাঁকিয়ে দেওয়ার এক অবাস্তব চেষ্টা। তাহের চেয়েছিলেন, তার ইচ্ছেরা যেন সময়কে গালিয়ে দেয়। অন্যদিকে খালেদ মোশাররফ, হুদা ও হায়দারের মতো বীররা ছিলেন বাস্তববাদী চেতনার স্তম্ভ। তারা জানতেন, দেশের মাটিকে রক্ষার জন্য সামরিক শৃঙ্খলা হলো মেরুদণ্ড। আমাদের ইতিহাসের পাতায় খালেদ মোশাররফ, নাজমুল হুদা, এবং এটিএম হায়দার হলেন অমর বীরত্বের প্রতীক। তারা ছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম সারির যোদ্ধা এবং সামরিক কৌশলের স্তম্ভ। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ (বীর-উত্তম) ছিলেন কে ফোর্সের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন একাত্তরের রণাঙ্গনের অন্যতম সেরা সামরিক মস্তিষ্ক। তার নেতৃত্ব ছিল দৃঢ়তা ও সাহসের মিশ্রণ, যা সৈন্যদের মধ্যে অদম্য প্রেরণা জোগাত। তার মতো সামরিক নেতা ছিলেন যেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বাণীর মতো, যিনি লেখেন, ‘বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা- বিপদে আমি না যেন করি ভয়।’ খালেদ মোশাররফ তার নেতৃত্ব দিয়ে সেই অভয় মন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
অন্যদিকে কর্নেল তাহেরের হৃদয়ের অস্থির আকাক্সক্ষা তাকে সামরিক শৃঙ্খলার পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। তার বিপ্লবী স্বপ্ন ছিল যেন রোমান্টিক উপন্যাসের এক আবেগপূর্ণ অধ্যায়, কিন্তু বাস্তবে তা ছিল ভ্রান্তির বালুচরে লেখা এক কবিতা। তাহেরের দোষ ছিল, তিনি ‘জনযুদ্ধের’ আবেগ দিয়ে একটি প্রশিক্ষিত সামরিক কাঠামো ভাঙতে চাইলেন। তার আহ্বান ছিল যেন এক ‘ক্রান্তিকালের বাঁশি’, যা শুধু আবেগী সৈনিকদের জাগাল, কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের জটিল অঙ্কটা বুঝতে পারল না।
খালেদ মোশাররফ সতর্ক করেছিলেন : ‘বিপ্লব তার সন্তানদের খেয়ে ফেলে।’ তার এই উক্তি ছিল যেন ভবিষ্যতের হলোগ্রাম, যা তাহেরের সামনে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি তা দেখতে অস্বীকার করলেন। তাহের এই সত্যের ছায়া উপেক্ষা করে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা (বিসোসে) গঠন করলেন। তার এই সিদ্ধান্ত ছিল যেন ‘নিজের কক্ষপথ ছেড়ে দূরে ছিটকে যাওয়া এক গ্রহ’- যা আর কক্ষপথে ফিরতে পারল না। তার এই সিদ্ধান্ত ছিল যেন কবি জীবনানন্দ দাশের ‘অদ্ভুত আঁধার’-এর পথে একাকী হেঁটে চলা, কিন্তু নক্ষত্রের ইশারা না মানা। এদিকে পঁচাত্তরে বীর খালেদ মোশাররফ মোশতাক সরকারকে হটিয়ে যে ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেন, তা ছিল জলের ওপর ভাসমান এক সিংহাসন, যা এক মুহূর্তের টানে তলিয়ে গেল।
তাহেরের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো তার নৈতিক স্খলন। তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বীরদের চরিত্র হনন করলেন। ৩ নভেম্বরের পর তিনি খালেদ মোশাররফকে ‘ভারতপন্থি’ বলে চিহ্নিত করলেন। অথচ যিনি বলেছিলেন : ‘যুদ্ধ শেষে বিজয়ী হলে কারা আমাদের পিঠে ছুরি মেরে শত্রু হবে, জানো? এই এরাই (ভারতীয় সেনারা)।’ এই মিথ্যাচার ছিল যেন ‘আয়নায় দেখা এক বিকৃত প্রতিচ্ছবি’, যেখানে সত্যের মুখ ঢাকা পড়েছিল। তাহেরের এই কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি কাপুরুষোচিত বিশ্বাসঘাতকতা। এই মিথ্যা ছিল যেন মুক্তির সেই পবিত্র পতাকাকেই কলঙ্কিত করা। তাহের আদর্শের চোখে খালেদ মোশাররফকে দেখতেন। খালেদ তখন তার কাছে মুক্তিযোদ্ধা নন, বরং ভারতপন্থি বুর্জোয়া অফিসার ছিলেন। তাহেরের মনে তখন বিপ্লবী জেদ ভর করেছিল। এটি ছিল যেন এক উপন্যাসের দৃশ্য- যেখানে নায়ক নিজেই নিজের ভাইকে ভুল বুঝে হত্যা করে। তাহের ভুলে গেলেন, খালেদের মাথায় একাত্তরের গোলাগুলির ক্ষত ছিল। তার বিপ্লবী তর্জনী দেখাল, ‘ঘরের শত্রু বিভীষণ।’ তাহেরের এই অন্ধবিশ্বাস ছিল খালেদের মৃত্যুপরোয়ানা।
মূলত তাহেরের এই আচরণ ছিল কাপুরুষোচিত, কারণ তিনি সামরিক নেতৃত্ব দেওয়ার নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি গোপন বিদ্রোহ বেছে নিলেন। তিনি ‘অফিসারের রক্ত চাই’ স্লোগান দিয়ে বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। সেই মন্ত্র ছিল যেন পাগলের হাতে ধারালো ছুরি তুলে দেওয়া। সেই ছুরি প্রথমে খালেদকে কাটল, আর তার এক সপ্তাহের মধ্যেই জিয়া সেই ছুরি উল্টো তাহেরের দিকেই ধরে তাকে ফাঁসিতে ঝোলালেন। এটি ছিল এক আয়নাঘর যেখানে এক বীরের মৃত্যু আরেক বীরের ফাঁসিকে অনিবার্য করে তুলল। তাহের যেন নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক অভিনেতা, যিনি মিথ্যা অভিনয় করতে বাধ্য হলেন। তিনি ছিলেন যেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসের সেই ট্র্যাজিক চরিত্র, যার ভালো উদ্দেশ্যও শেষ পর্যন্ত কেবল বিষফলই জন্ম দেয়।
তাহেরের উচ্চাভিলাষ যখন ৭ নভেম্বরের সিপাহি বিদ্রোহে রূপ নিল, তখন সেই বিপ্লবী আগুন দ্রুতই তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। এই নৈরাজ্য ছিল যেন এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের সেই পাগল চায়ের পার্টির মতো- যেখানে কোনো নিয়ম মানা হচ্ছিল না। এই নিয়ন্ত্রণহীন বিশৃঙ্খলার নির্মম শিকার হলেন সেই তিন বীর- খালেদ মোশাররফ, হুদা ও হায়দার। তাদের এই হত্যাকাণ্ড ছিল তাহেরের সৃষ্ট নৈরাজ্যের প্রত্যক্ষ ফল।
বিখ্যাত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায় বলা যায়, এই মৃত্যু ছিল যেন ‘এ জীবন বড় বেশি ফোঁটা’, যা অকালে ঝরে গেল। এই রক্তপাত প্রমাণ করে যে, খালেদ মোশাররফের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হলো- ‘বিপ্লব তার সন্তানদেরই খেয়ে ফেলে।’ তাহেরের স্বপ্নভঙ্গের মূল্য দিতে হলো এই তিন জাতীয় বীরকে তাদের রক্তের বিনিময়ে।
এই চরম বিশৃঙ্খলা এবং তাহেরের হিসাব-নিকাশের ভুলের কারণেই মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের উত্থান ছিল ঐতিহাসিক নিয়তির মতো অনিবার্য। জিয়া এই বিদ্রোহের সরাসরি সুবিধাভোগী হলেন। জিয়া যেন দাবার বোর্ডে অপেক্ষমাণ এক চালক, যিনি তাহেরের ভুল চালের সুযোগ নিলেন। জিয়া দ্রুততার সঙ্গে বুঝতে পারলেন যে তাহেরের নৈরাজ্যই তাকে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার সুযোগ করে দিয়েছে।
জিয়াউর রহমান সামরিক শৃঙ্খলার নামে তাহেরের বিপ্লবী দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন। তাহেরের ফাঁসি ছিল জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক কৌশলের এক চূড়ান্ত পদক্ষেপ। জিয়া তাহেরের উচ্চাভিলাষকে সামরিক আইনের অধীনে এনে বিচার করলেন। এই বিচার ছিল সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রতীকী বার্তা। এই ঘটনায় জিয়াউর রহমান রাজনৈতিকভাবে দায়মুক্ত হলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শেষের কবিতা’র মতো, এখানেও নিয়তি এক অদৃশ্য বাঁধনে সব চরিত্রকে টেনে আনল। সিপাহি সংহতির ৫০ বছর পরও এই অনুচ্চারিত বিলাপ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, হৃদয়ের আবেগ দিয়ে নয়, বাস্তব কঠিন কষ্টিপাথরে যাচাই করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়।
আরও পড়ুন:
মার্কিন শ্রমনীতি দেশের জন্য কতটুকু প্রযোজ্য?
রাফসান আহমেদ : নৃবিজ্ঞানী, দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক গবেষক এবং চলচ্চিত্রকার
মতামত লেখকের নিজস্ব